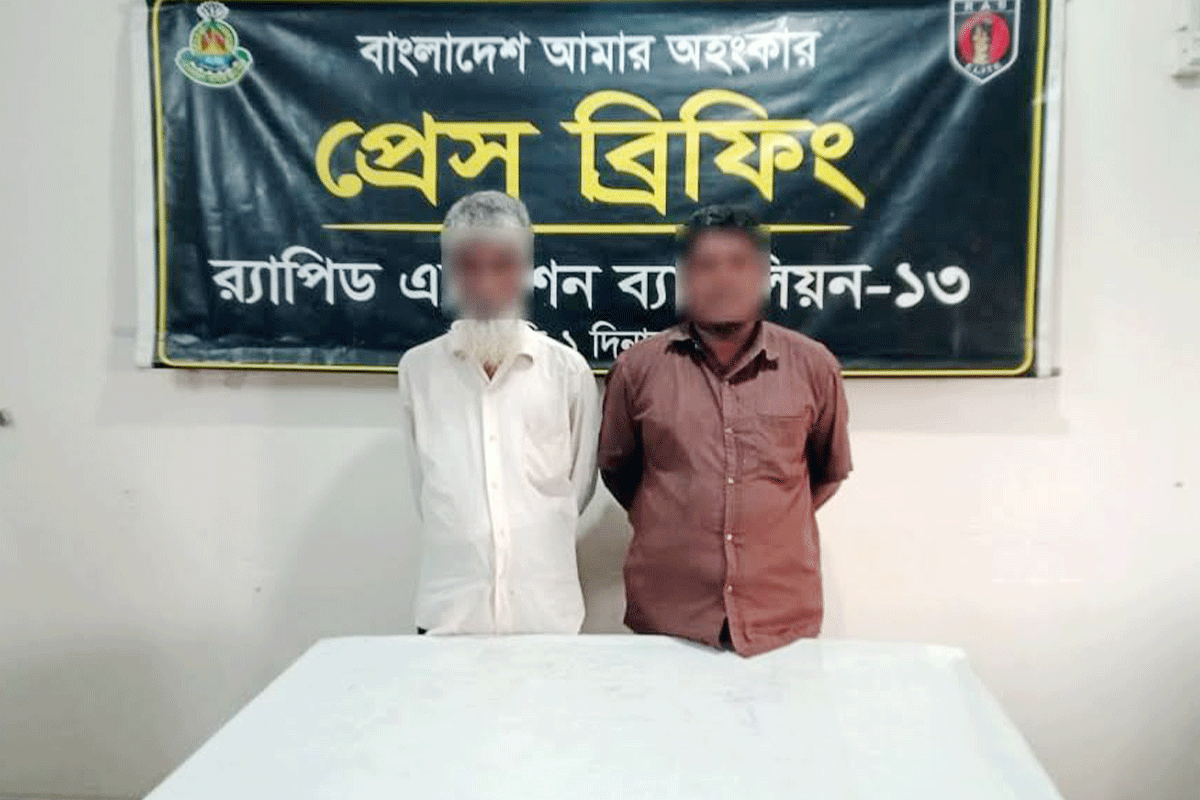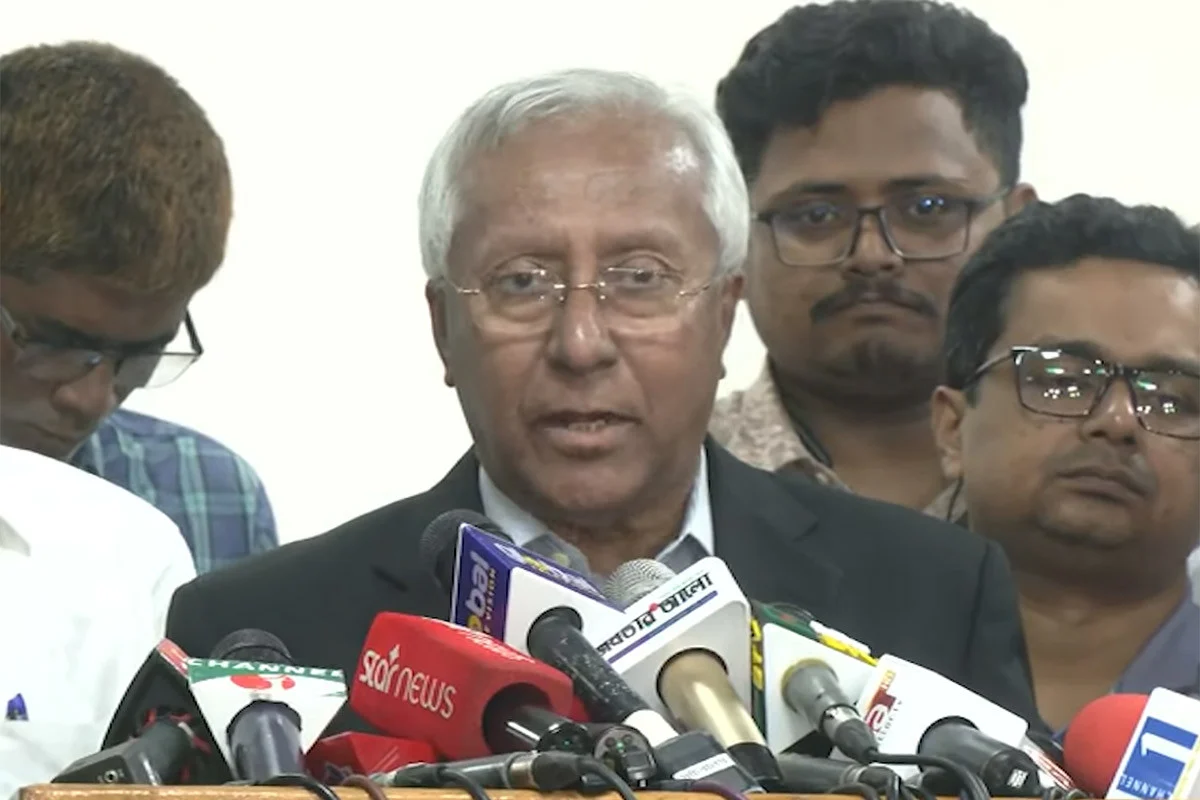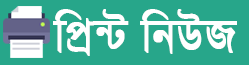
ঘটনার সত্যতা যাচাই করা একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। থানা-পুলিশ থেকে শুরু করে আদালত—সব মিলিয়ে একটি মামলার রায় হতে বছর বছর কেটে যায়। সেই সময়ের মধ্যে অসংখ্য সাক্ষী বদলে যায়, প্রমাণ হারিয়ে যায় কিংবা নতুন তথ্য যোগ হয়।
অথচ একজন সাংবাদিককে একই ঘটনার খবর লিখতে হয় মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভেতরে। কারণ সংবাদ হলো চলমান সময়ের প্রতিচ্ছবি, যা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হয় সঙ্গে সঙ্গেই। এখানেই সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
একজন সাংবাদিকের কাজ কেবল খবর লেখা নয়, বরং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। কিন্তু তার হাতে সময় থাকে অতি সীমিত। তিনি পুলিশ বা আদালতের মতো দীর্ঘ তদন্তের সুযোগ পান না।
অনেক সময় সাংবাদিককে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে কথা বলে বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। এ অবস্থায় শতভাগ সত্যতা নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হলেও সাংবাদিকের প্রচেষ্টা থাকে ঘটনাটির প্রকৃত চিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরার।
সমাজে প্রায়ই বলা হয়—“সাংবাদিকের সংবাদে শতভাগ সত্য থাকতে হবে।” কথাটি শুনতে ভালো লাগলেও বাস্তবে এর ভিন্নতা রয়েছে। কারণ সংবাদ তৈরি হয় চলমান তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। একদিনের তথ্যের সাথে পরদিনের তথ্য ভিন্ন হতে পারে। আদালতের চূড়ান্ত রায় আসতে পারে একেবারেই অন্য রকম।
তাই সংবাদকে একেবারে রায়ের মতো বিচার করা ঠিক নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সাংবাদিকতার অবদান অনস্বীকার্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাংবাদিকরা তাদের কলম ও ক্যামেরা দিয়ে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছেন পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা। বিদেশি গণমাধ্যমে প্রচারিত সেইসব প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করেছিল।
স্বাধীনতার পর থেকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রাম কিংবা সাম্প্রতিক দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন—সব ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। তাদের কাজ কেবল তথ্য দেওয়া নয়, বরং জনমত গঠন করা। একটি শক্তিশালী জনমত অনেক সময় রাষ্ট্রের নীতিকে পরিবর্তন করেছে। সাংবাদিকরা অন্ধকারে আলো জ্বালিয়েছেন, নির্যাতিতের আর্তনাদ পৌঁছে দিয়েছেন রাষ্ট্রের দরজায়।
অথচ এই পথ চলা কখনোই ছিল না সহজ। বহু সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য—একজন সাংবাদিকের একটি ছোট ভুলকে সমাজ বড় করে দেখে। অথচ আমরা দেখি, চিকিৎসক, আইনজীবী কিংবা প্রশাসনের ভুলেও বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হয়, তবুও তাদের প্রতি একইভাবে অভিযোগ তুলতে অনেকে ইতস্তত করেন। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে যেন এক ধরনের ভিন্ন মানদণ্ড তৈরি হয়ে গেছে।
এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার, সাংবাদিকরাও মানুষ। তাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। সবসময় সব সূত্র পাওয়া যায় না, সব তথ্য যাচাই করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাংবাদিক ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা লিখছেন। বরং দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি চেষ্টা করেন সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। পাঠকের উচিত সেই প্রচেষ্টাকে সম্মানের চোখে দেখা। সাংবাদিকরা যদি কলম নামিয়ে রাখেন, তবে সমাজ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।
মানুষ জানবে না কে কোথায় অন্যায় করছে, কে দুর্নীতিতে জড়িত, কিংবা কোথায় মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমই হলো সমাজের আয়না। সেই আয়না যদি ভেঙে যায়, তাহলে রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তথ্যের যুগে সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ায় দ্রুত, কিন্তু তার সত্যতা যাচাই করে সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় কেবল সাংবাদিকরাই। তাই সাংবাদিককে অবমূল্যায়ন করা মানে গুজবের কাছে সমাজকে সমর্পণ করা। আজকের দিনে সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত নানা চাপের মুখে কাজ করেন।
রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক সংকট, নিরাপত্তাহীনতা—সবকিছু সামলেই তারা মানুষের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করেন। অনেক সময় তাদের ওপর হামলা হয়, মামলা দেওয়া হয়, হুমকি দেওয়া হয়। তবুও তারা দায়িত্ব পালন করে যান। তাই সমাজের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো সাংবাদিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করা এবং তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করা।
গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে মুক্ত সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে রাষ্ট্র কখনোই জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে না। সাংবাদিকরা প্রশ্ন না করলে দুর্নীতি বাড়বে, অন্যায় চেপে যাবে। তাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। সাংবাদিকতা কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। তারা সমাজের চোখ, কান ও কণ্ঠস্বর।
ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকের কাজই সমাজকে এগিয়ে নেয়, অন্যায় প্রকাশ করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। তাই সাংবাদিকদের অবমূল্যায়ন নয়, সম্মানই হওয়া উচিত আমাদের প্রধান কর্তব্য।

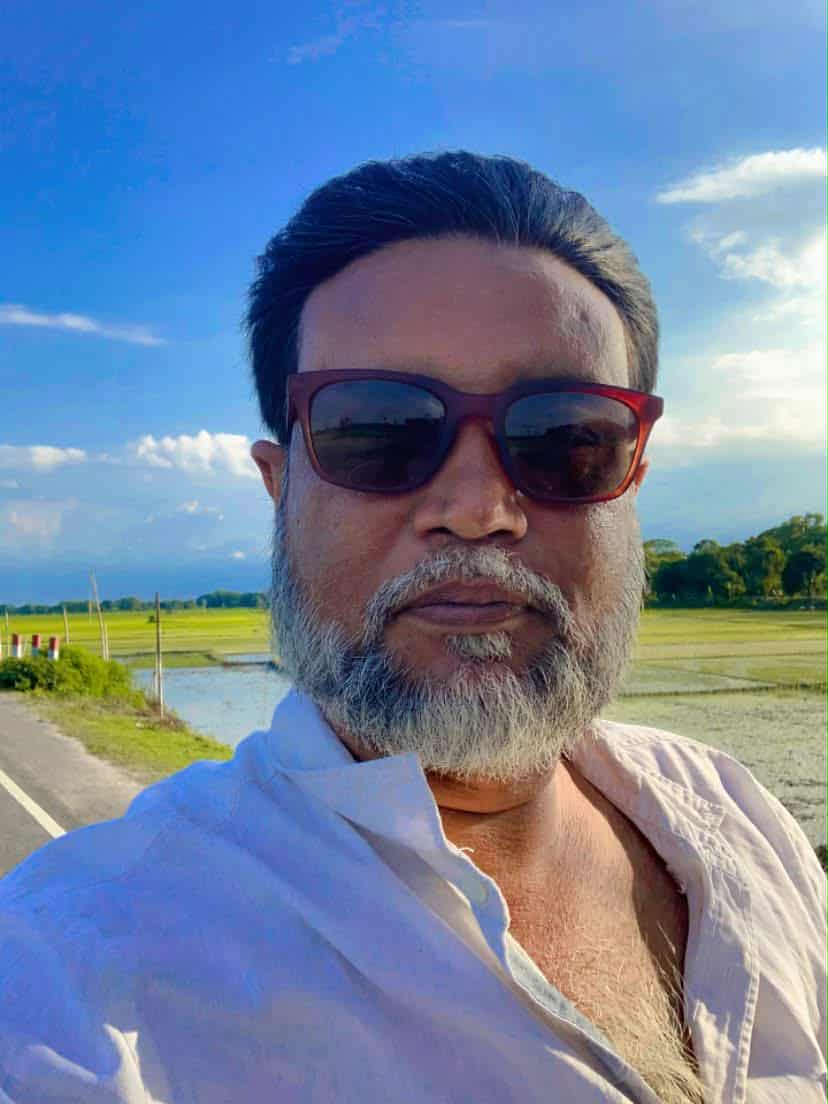 শাহ আলী তৌফিক রিপন, ষ্টাপ রিপোর্টার
শাহ আলী তৌফিক রিপন, ষ্টাপ রিপোর্টার